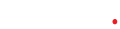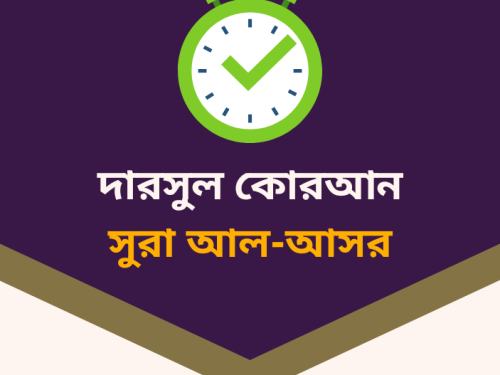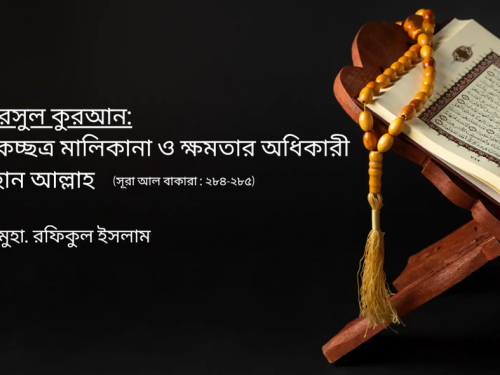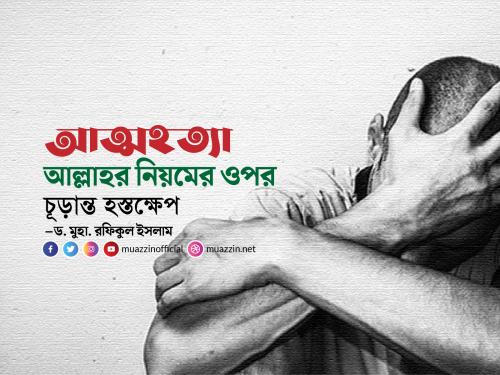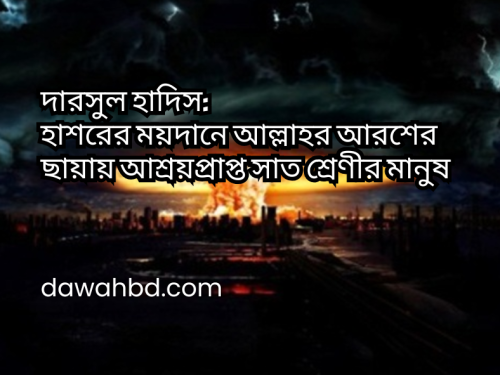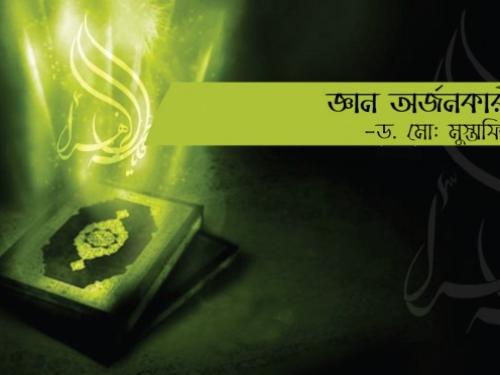১। কালের শপথ / সময়ের কসম।
২। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
৩। কিন্ত তারা বাদে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হকের নির্দেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য ধরার নির্দেশ দেয়।
আলোচ্য বিষয় : মানুষের সফলতা বিফলতা এবং ধ্বংশের পথ কোনটি তাহা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে।
নাযিলের সময় ও ক্রম: মাক্কী সূরা। মক্কা জীবনের প্রথম অধ্যায়ে নাযিলকৃত। নাযিলের ক্রমানুসারে ১৩ নং সূরা। এর আগে পর্যায়ক্রমে সূরা লাইল (রাত), সূরা ফাজর (ঊষা), সূরা দুহা (পূর্বাহ্ণ কিরণ) এবং ইনশিরাহ (উন্মুক্তকরণ) নাযিল হয়। রাত, উষা ও পূর্বাহ্ণ এর পরই তো আসরের সময় হয়।
আয়াতভিত্তিক ব্যাখ্যা:
১.
وَٱلْعَصْرِ
অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার,আয়াতটির অর্থ করেছেন, সময়ের/যুগের/কালের/মহাকালের শপথ/কসম! এখানে আয়াতের শুরুতে ‘ওয়া’ হল হরফে যার বা অব্যয়। সাধারণত ‘ওয়া’ অর্থ ‘এবং’। দুটি শব্দ, বাক্য কিংবা ভাবকে যুক্ত করতে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে কসম বা শপথ অর্থেও বাক্যের শুরুতে ওয়া’র ব্যবহার বিদিত। একই ভঙ্গিতে কুর’আনের ২৩ টি সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এই ধরণের শপথ করেছেন। এর মধ্যে ১৭ টি সূরা ‘ওয়া’ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে এটি কুর’আনের বা আল্লাহ তায়ালার নসিহতের একটি কমন স্টাইল। লক্ষ্যণীয়, আল্লাহ নিজের নামে শপথ না নিয়ে সৃষ্টির নামে কসম করেন কেন? সৃষ্টিকে গ্লোরিফাই করার জন্য, এর মাধ্যমে তো স্রষ্টা নিজেকেই গ্লোরিফাই করেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনার আগে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে, অথবা সাক্ষী হাজির করতে অথবা এটি বুঝাতে যে এই বিষয়গুলো তোমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশের অংশ, এসব সম্পর্কে তোমাদের জানাশোনা আছে বা পরিচিত, তারাও তো আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন বহন করে। আল্লাহ তায়ালা এখানে সময়ের কসম খেয়ে সময়ের গুরুত্বও বুঝিয়েছেন, পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যের সাপেক্ষে সময়কে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেছেন। আবার আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
আসর শব্দের অর্থ ইমাম মালিক করেছেন আসরের সালাতের সময়। ইবনে আব্বাস বলছেন, পড়ন্ত বেলা বা ক্ষয়িষ্ণু সময় (declining time), মানবজীবনের বৃদ্ধকাল, সময়ের কাঠিন্য বা কষ্টকর সময়। ইবনে কাসিরের মতে, যে কাল/সময়ে মানুষ সৎ/পাপ কর্ম করে। ইমাম ফারাহি আরবি প্রাচীন সাহিত্যে কবি ইমরুল কায়েস ও কবি ওবায়েদের কবিতায় আসর শব্দের উল্লেখ করে এর একটি অর্থ করেছেন ‘অতীতে ঘটে যাওয়া নির্দিষ্ট সময় কাল’ (period of time)। আরেকটি মত হল, আসর মানে সময়ের ক্ষণস্থায়িত্ব, ভঙ্গুরতা, ধাবমানতা (briskness & swiftness of time)। অনেকেই আসর অর্থ যুগ বা মহাকাল করেছে কিন্তু আসর মানে সময়ের খুবই ক্ষুদ্রাংশ (fraction of time) বা একটি মুহূর্ত, সময়ের সামগ্রিকতা (totality of time) বুঝাতে কুর’আনে ‘দাহর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
هَلۡ اَتٰی عَلَی الۡاِنۡسَانِ حِیۡنٌ مِّنَ الدَّهۡرِ لَمۡ یَكُنۡ شَیۡئًا مَّذۡكُوۡرًا
“মহাকালের মধ্য হতে মানুষের উপর কি এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখ করার যোগ্য কোন বস্তুই ছিল না?” (দাহর ১) আবার হাদিসে বলা হয়েছে, لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر তোমরা যুগকে গালি দিও না। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই যুগ। (মুসলিম ২২৪৬)
রিসালায়ে নুরে সাইয়েদ নুরসি লিখেছেন, ফজর সময়টা হল বসন্তের শুরু, মাতৃগর্ভে মানুষের আগমন, ছয়দিনে যে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টি সম্পন্ন করেছিলেন তার ১ম দিন, এবং সেই সময় যখন মানুষের উপর জান্নাতের নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে। যোহর মানে গ্রীষ্মকালের মধ্য সময়, মানুষের যৌবন ও তারুণ্য, দুনিয়াতে মানুষের পদার্পণ এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা করা ও অসীম অনুগ্রহ প্রদান করা। আসর অর্থ বিষণ্ণ শরৎকাল, মানুষের শোকাতুর-নিরানন্দ বৃদ্ধকাল, মুহাম্মদ সা. এর নবুয়তকাল ও তাদের উপর নাযিল হওয়া শরিয়ত ও আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, দিনের শেষে ব্যবসা বা দিনমজুরের হিসাব নিকাশের সময়, আল্লাহ তায়ালার কাছেও ফেরেশতাদের রিপোর্টিং এর সময় মানুষের ভালো-মন্দ, স্বাস্থ্য, জীবিকা প্রভৃতি বিষয়ে । মাগরিব বলতে বুঝায়, যেমন সূর্য ডুবে যায় তেমনি শরৎকাল শেষে অনেক প্রাণীর বিদায় ঘটে, মানুষের মৃত্যু, দুনিয়া ধ্বংস বা কিয়ামতের শুরু, আল্লাহর মহত্ব ও পরম হওয়ার বহিঃপ্রকাশ। এশার সময় হল শীতকালের ন্যায় জরা ও জবুথবুতা, কবরের নিস্তব্ধতা, কিয়ামতের পরে পুরা সৃষ্টিজগতের নিস্তব্ধতা। তাহাজ্জুদের সময়ে শীতকালের মধ্যে ক্ষণিক উষ্ণতা, কবরে একটু আলোর ব্যবস্থা, শেষবিচারে মানুষের উত্থান, আল্লাহর রহম ও ক্ষমার প্রতি মানুষের ব্যাকুলতা। সাইয়েদ নুরসি সময়ের ব্যাখ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমাদের পৃথিবীর ১ দিন আল্লাহ তায়ালার মহাকালের ঘড়ির ১ সেকেন্ডের সদৃশ, কয়েক বছরে ১ মিনিট… এই হিসাব করলে হাশরের একদিন যে ৫০ হাজার বছরের সমান তা অনুমান করা যায়।
বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা জানি, প্রসঙ্গ কাঠামো বদলে গেলে সময় ও দূরত্ব বা ব্যাপ্তির পরিবর্তন হয়। আইনস্টাইনের মতে, পরম সময় বলে কিছু নেই। কিন্তু নিউটন ধর্ম ও দর্শনের মতো করে পরম সময় নিয়ে ভেবেছিলেন। তাঁর মতে, পরম সময় “বাহ্যিক কিছুর সাথে সম্পর্ক ছাড়াই সমানভাবে প্রবাহিত হয়” ( প্রিন্সিপিয়া, 1687)। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সময়ের গণনা শুরু হয় ‘বিগ ব্যাঙ’ (Big Bang) থেকে। এর আগে সময় বা t=0 ছিল। এটি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যে, বিজ্ঞান বিগ ব্যাঙের আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিকে সময় ও ব্যাপ্তির সাপেক্ষে সম্পৃক্ত বা বর্ণনা করতে পারেনি। তাই সময়ের পরমতা সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা নেই। মুসলিম চিন্তাবিদ যেমন আল-ফারাবি (873 – 950) এবং ইবনে সিনা (980 – 1037) মনে করেছিলেন যে, সৃষ্টির কাজটিকে অপার্থিব (স্থায়ী) এবং সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক হিসাবে কল্পনা করা উচিত। মূলত, সময় ব্যাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, স্বাধীন ও মৌলিক। বিজ্ঞান অনুযায়ী জগত চতুর্মাত্রিক। ব্যাপ্তির ৩ মাত্রার সাথে সময়ের ১ মাত্রা যোগ করে হয় ৪ মাত্রা। ফলে পদার্থবিদ্যার সূত্রানুসারে বাম, ডান কিংবা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, বাম-ডানের মধ্যে যদি রদবদল করা হয়, তাহলে দুনিয়ার তাবৎ বাঁহাতি মানুষ ডানহাতি হবে, বুকের বামপাশের হৃদযন্ত্র ডানপাশে অবস্থান নেবে। এতে খুব বেশি অসুবিধা না হলেও অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যদি রদবদল হয়, তাহলে কী মহাকাণ্ড ঘটবে চিন্তা করুন। ঠিক টাইম ট্রাভেলের ফিকশনের মতো ঘটনা ঘটবে (আল কুর’আনে বিজ্ঞান, ২০০৪)। তবে এখান থেকে একটা ব্যাপার অনুমান করা যায়, হাশরের ময়দানে কোন মানুষকে যখন তার দুনিয়ার আমলনামা দেখানো হবে, তখন সময়ের ডাইমেনশন উল্টে দিয়ে হয়ত তাকে দুনিয়ার জীবনে টাইম ট্রাভেল করানো হতে পারে।
عَصْر শব্দটি ‘আইন-সোয়াদ-রা’ ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু সময়। এই ধাতু আল কুর’আনে ৪টি রূপে ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আসর শব্দের প্রকৃত ধারণা পাওয়ার জন্য অন্য ৪ টি বর্ণনা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।
১. ই’সরু الدهروَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیٰنِ١ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا١َۚ َ
কারাগারে তার সাথে আরো দু’টি ভৃত্যও প্রবেশ করলো। একদিন তাদের একজন তাঁকে বললো, “আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মদ নিংড়ে বের করছি।” (ইউসুফ ৩৬)
৩. ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِیْهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیْهِ یَعْصِرُوْنَ۠
এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।” (ইউসুফ ৪৯)
৪. মু’সিরাত وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًاۙ
আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা। (নাবা ১৪)
সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াতে ই’সরু মানে ঝঞ্ঝাবায়ু যার মধ্যে আগুনের হলকা আছে। সূরা নাবার ১৪ নং আয়াতে মু’সিরাত বলতে মেঘমালা বলা হচ্ছে, এমন মেঘ যা বৃষ্টিতে টইটুম্বুর কিন্তু এখনও বৃষ্টিপাত শুরু হয়নি। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন বৃষ্টিবাহী বাতাস, কেউ বলেছেন আকাশ। ইমাম কুরতুবি বলেছেন, আরবিতে সেই কুমারী কন্যাকে মু’সিরাত বলা হয় যে সাবালিকা হয়েছে বা ঋতুস্রাবের সময় সমাগত কিন্তু এখনও স্রাব শুরু হয়নি। এসময় নারীরা ঘরে আশ্রয় নেয় সেজন্যও তাদের মু’সিরাত বলা হয়। তাই মু’সিরাতের আরেক অর্থ- আশ্রয়স্থল। সূরা ইউসুফের উল্লেখ্য ২ টি আয়াতেই ধাতুটি নিংড়ানো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। টসটসে তাজা ফলাদি থেকে রস নিংড়ানো। আসর শব্দটির ধাতুভিত্তিক এই অর্থগুলো সামনে রেখে আমরা সূরা আসরের ১ম আয়াতের অর্থ নিম্নরূপে অনুধাবন করতে পারি-
১. ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের কসম বা পতনশীল, ধ্বংসকারী সময়ের কসম। এই অর্থ নিলেও পরের আয়াতে মানুষের ক্ষতি বা ধ্বংসে নিপতিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।
২. বৃষ্টি ধারণকারী মেঘ, বৃষ্টিবাহী বাতাস, ঋতু সম্ভাবী নারী কিংবা আশ্রয়স্থল এসব অর্থই উৎপাদনমুখী, কল্যাণময়তার প্রতীক। তাই সময়কে যদি দ্বিধারী তলোয়ার চিন্তা করা হয় যার একধার ধ্বংসাত্মক, অন্যধার প্রোডাক্টিভ বা নেয়ামতপূর্ণ। তাহলে আয়াতের ভাব দাঁড়ায়, প্রোডাক্টিভ/উৎপাদনমুখী/কল্যাণময় সময়ের শপথ। ফলে ২য় আয়াতের সাথে বিপরীতভাবে যুক্ত হয়, যে বা যারা এই কল্যাণময় সময়ের সদ্ব্যবহার করবে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আবার সময় ভালো-মন্দ সবকিছু ধারণ করে সেই অর্থও করা যায়- ভালো-মন্দ/পাপ-পুণ্য ধারণকারী সময়ের শপথ যা ইবনে কাসিরের মন্তব্যের সাথে মিলে যায়।
৩. নিংড়ানো অর্থ যদি নেয়া হয় তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, সময় বা ইতিহাস নিংড়ে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ বরাবর ক্ষতির মধ্যে নিবিষ্ট। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেছেন, আল্লাহ সময়ের কসম খেয়ে তাঁর দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে বলেছেন। আল্লাহর দিনগুলো যেমন- আদম আ. এর সৃষ্টি, নুহ আ. এর প্লাবন, ইবরাহিম আ.কে আগুন থেকে রক্ষা, লুত আ. ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য জাতির উপর নাযিল হওয়া গজবে দিনগুলো, রাসুল সা. এর উপর কুর’আন নাযিল, বদর-উহুদ-মুতা-হুনায়েন প্রভৃতি দিনসমূহের দিকে তাকালে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও সফল ব্যক্তিদের নমুনা দেখতে পাবো। ইমাম ফারাহিও মনে করেন, ঐতিহাসিক দিন ও স্থানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- পিরামিড, আদ ও সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ, ডেড সি ইত্যাদি দেখে আমরা বুঝতে পারব সময়ের পরিক্রমায় আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।
আসরের সময়টি দিনের সংকটপূর্ণ সময়, জরুরি অবস্থা, দিনের শেষ অবস্থা, শেষ সালাত। আসরের ইমার্জেন্সি বুঝাতে অধিকাংশ তাফসিরসমূহে বরফওয়ালার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে এনোনাইমাস ভাবে। কিন্তু এই উপমাটি ইমাম রাজি তাঁর তাফসিরে কবিরে উল্লেখ করেছেন। আসলে ভবিষ্যতের উদর থেকে যে মুহূর্তটি বের হয়ে এখনই অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল তাই ‘আসর’। এই বিলীন হওয়া মানে অবিশ্বাসীরা মনে করে হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, হিসাবের উর্ধ্বে চলে যাওয়া মনে করে। কিন্তু সূরা আসরে সেটি মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে, সময় নিয়ে মানুষের এই ভাবনা চিন্তার ভ্রষ্টতা বা দৈনতা। সময় আসলে আল্লাহ তায়ালার করতলগত। এর রেকর্ড রাখা হয়, জবাবদিহিতা করতে হবে।
২নং আয়াত:
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍۙ নিশ্চয়/নিঃসন্দেহে মানুষ/মানবজাতি (অবশ্যই) ক্ষতিগ্রস্ত
ইন্না+আল+ইনসানা+লা+ফি+খুসর। আয়াতটি বিশেষ্য প্রধান, ক্রিয়া প্রধান নয়। বিশেষ্য প্রধান (জুমলাহ ইসমিয়্যাহ) বৈশিষ্ট্যের কারণে বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চাবি শব্দ দুটি বাদ দিলে বাকি অব্যয় চারটি (ইন্না, আল, লা, ফি) বক্তব্য জোরালো ও চিরস্থির বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ইন্না (নিশ্চয়/Certainty অর্থে) হারফুন নাসব বা পদান্বয়ী অব্যয়। ‘আল’ শব্দটি ইংরেজি The এর মতো নির্দেশক (determiner) অর্থে। যেমন মানবদেহে অনেকগুলো পর্দা বা diaphragm আছে, কিন্তু The diaphragm বললে কেবল মধ্যচ্ছদা পর্দা বুঝায় যা বুক ও পেটের সীমানা নির্ধারণ করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কাজে লাগে। ‘লা’ শব্দটিকে বলা হয় আরবিতে লাম তাকিদ অর্থাৎ তাগিদ অর্থে (জোর) ব্যবহার হয়। ‘ফি’ একটি হারফুন জার বা অব্যয়, যেটি মধ্যে (নিশ্চিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন দেখুন ছোট্ট একটি আয়াতে দুটি শব্দের বিপরীতে দুটি করে চারটি তাকিদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই কথাটি এতটাই গুরুত্ববহ ও অবশ্যম্ভাবী।
ইনসান (মানুষ) শব্দটি বিশেষ্য ও এক বচনে বর্ণিত, বহুবচনে নাস । আবার বর্ণনার ধাঁচ পুরো মানবজাতিও লক্ষ্য। তাই পরবর্তী চারটি হুকুম ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে পালন করতে হবে। মানুষ তাই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত। ইনসান শব্দটি দুটি ধাতু থেকে এসেছে মনে করা হয়- ১. ‘নাসিয়া’ মানে ভুলে যাওয়া ২. ‘ইনস’ অর্থ কোমল, সামাজিক। কুর’আনে ইনসান শব্দটি ৭১ বার, নাস শব্দটি ২৪১ বার এসেছে। ইনসান ও নাস নামে দুটি সূরাও আছে। মানুষ শব্দের আরেকটি অর্থ বাশার, যেমন- আদম আ.কে আবুল বাশার বা মানবজাতির পিতা বলা হয়। প্রশ্ন হল এইখানে বাশার শব্দও তো ব্যবহার করা যেত, ইনসান শব্দ কেন আনা হল। বাশার শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল কোমল বা মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট প্রাণী। পৃথিবীতে মানুষই কেবল কোমল ত্বকের অধিকারী ও অনন্য। এটি মানুষের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য। তাই কুর’আনে যেখানে মানুষের অবয়বগত মিল বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে সেখানে বাশার শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন- قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوْحٰۤى”
বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয়” (কাহাফ ১১০)
আর যখন মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, আচরণ ইত্যাদি উচ্চমার্গীয় ভূমিকার বর্ণনা আলোকপাত করা হয়, তখন ইনসান শব্দটি আনা হয়। আলোচ্য সূরাতে যেহেতু উপর্যুক্ত বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে তাই ইনসান শব্দ আনা হয়েছে। এখন ইনসান শব্দের দুটি ধাতুভিত্তিক অর্থকে আমলে নিলে দেখা যায়- মানুষ ভুলে গেছে তার অবস্থান, সম্মান, শপথ ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিধায় সে ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে। মানুষ রুহের জগতে তার রবের কাছে করা ওয়াদা ভুলে গেছে। মানুষের জান ও মাল আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, সেটিও ভুলে গেছে সে। আগের আয়াতের সাথে রিলেট করে দেখুন- সেই সময়ের শপথ যার ব্যবধানে মানুষ ভুলে যায়। আমাদের আল্লাহর কাছে থেকে দুনিয়ায় আসা ও ফেরত যাওয়ার বিভিন্ন ধাপে আমরা ভুলে যাই। এটি মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, প্রমাণ করে দিতে হয়। আরেকটি ভাব নেয়া যায়- নিশ্চয় (ভুলো মনের) মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত। وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ١ؕ ” তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন” (হাশর ১৯)। ইবনে আব্বাসের অর্থানুযায়ী, আসর মানে মানুষের বৃদ্ধকাল (old age) যদি ধরি, তাহলে এসময় মানুষের প্রধান দুর্ভোগ কী? তা হল ভুলে যাওয়া (dementia’র অন্যতম লক্ষণ)। তাহলে সেই পীড়িত অবস্থার কসম করে আল্লাহ মানুষকে তার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করেছেন।
আবার ‘ইনস’ ধাতুর কোমল, সমাজবদ্ধ বা সামাজিক (social) অর্থ গ্রহণ করলে পরের আয়াতে দ্রষ্টব্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। ৩ নং আয়াতে যে ৪ টি দায়িত্বের উল্লেখ আছে প্রতিটিই সমাজের জন্য জরুরি। সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সমাজকে সঠিক পথে চলমান ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে উক্ত গুণাবলি একান্ত দরকারি। সেক্ষেত্রে সামাজিক মানুষের দায়িত্ব সমাজ সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো, নতুবা সে বা তারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আয়াতে উল্লিখিত ইনসান বলতে অনেক সালাফ আবার কাফিরদের বুঝিয়েছেন, কেননা পরের আয়াতে ঈমানদারকে এর ব্যতিক্রম ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
ইনসানের কিছু বৈশিষ্ট্য জানা যাক-
১. মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (নিসা ২৮)
২. বিপদে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, বিপদ কেটে গেলে আত্ম-অহমিকায় ভোগে। (ইউনুস ১২)
৩. আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার পর বঞ্চিত হলে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়। (হুদ ৯)
৪. নিশ্চয় মানুষ জালেম ও অস্বীকারকারী। (ইবরাহিম ৩৪, হজ ৬৬)
৫. কলহপ্রিয়। (নাহল ৪, কাহাফ ৫৪)
৬. মানুষ অকল্যাণ কামনা করে সেভাবে-যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই দ্রুতকামী। (ইসরা ১১, আম্বিয়া ৩৭)
৭. অকৃজ্ঞ (ইসরা ৬৭)। রবের প্রতি অকৃজ্ঞ। (আদিয়াত ৬)
৮. বড়ই সংকীর্ণমনা। (ইসরা ১০০)
৯. মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। (আলাক ৬)
তাহলে মানুষের এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে রাখলে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ অনেকটাই সুস্পষ্ট। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কারণ সে অস্বীকারকারী, অকৃতজ্ঞ, কলহপ্রিয়, সংকীর্ণমনা, সীমালঙ্ঘনকারী, ত্বরাপ্রবণ। মানুষ অস্বীকারকারী (মূল ইবারতে সবস্থানে কাফুরা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে), তাই তাকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সংকীর্ণমনা, সীমালঙ্ঘনকারী তাই আমলে সালেহ করার কথা বলা হয়েছে। হকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হতাশ, কলহপ্রিয়, ত্বরাপ্রবণ, দূর্বল তাই পরস্পরকে হক ও সবরের উপদেশ দিতে বলা হয়েছে।
খুসরিন অর্থ ক্ষতি যা লাভ ব্য সফলতার বিপরীত। এখানে বিশেষ্য রূপে শব্দটি এসেছে, অথচ ক্রিয়া রূপে ‘লা খাসির’ বা ‘লাকাদ খাসিরা’ এইভাবে বলতে পারতেন। মূল উদ্দেশ্য একটাই জোর দেয়া ও নি:সন্দেহ বুঝাতে এটি আনা হয়েছে। খুসর শব্দটি ‘খা-সিন-রা’ ধাতু থেকে উৎপন্ন যা ১০ টি রূপে ৬৫ বার কুর’আনে এসেছে। কুর’আনে ক্ষতির তীব্রতা বুঝাতে ৪টি রূপকে বেছে নেয়া হয়েছে।
১। খুসর/খুসরিন: অর্থাৎ প্রচণ্ড/ভীষণ/ভয়ানক ক্ষতি। তাহলে মানুষ নিঃসন্দেহে ভয়ানক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।
২। খাসা-রা: যখন কেউ ক্ষতির মধ্যে আছে এবং সেই ক্ষতি বা দুর্ভোগ আরও বাড়ানো হচ্ছে। (ইসরা ৮২, নুহ ২১)
৩। আখসার: সর্বাধিক ক্ষতি। (হুদ ২২, কাহাফ ১০৩)
৪। খুসরান: চূড়ান্ত ক্ষতি। (হজ ১১, তালাক ৮)
খুসর শব্দের অর্থ আল-আখফাশ করেছেন, সাধারণ অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু; আল-ফাররা এর মতে, ভয়াবহ পরিণতি। ইবনে জায়েদের মতে, মন্দ কর্ম। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় নিশ্চয় মানুষ মন্দ কর্মে নিমজ্জিত। খুসর এর আরেকটি অর্থ ব্যাবসাতে দেউলিয়া হওয়া। সূরা সফ থেকে আমরা জানি, আল্লাহর পথে জীবন (সময়) ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা অতি উত্তম ব্যাবসা। আবার এই উত্তম ব্যাবসার কথা সূরা জুমুয়ার শেষ আয়াতেও বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সময়ের কসম দিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, মানুষ বরাবর এই ব্যাবসায়ে দেউলিয়া হয়ে বসে আছে অথচ নিম্নোক্ত ৪টি কাজের মাধ্যমে সে সফল হতে পারে। আল্লাহু আ’লাম।
কুর’আনে ক্ষতির তালিকায় কারা আছে?
১. কুর’আন জালিমদের জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি করে (অস্বীকার, অবমাননা করার কারণে। (ইসরা ৮২)
২. কুফরির কারণে কাফিরদের ক্ষতি বৃদ্ধি পাবে। (ফাতির ৩৯)
৩. সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। (নুহ ২১)
৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা (তালাক ৮)
৫। যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে। (নিসা ১১৯)
৬. কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করা (আনয়াম ১২)
৭. কিতাবকে অস্বীকার করা। (আনয়াম ২০)
৮. যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সাক্ষাতের ঘোষণাকে মিথ্যা গণ্য করেছে। (আনয়াম ৩১, ইউনুস ৪৫)
৯. যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে। (আনয়াম ১৪০)
১০. যাদের মিজান বা পাল্লা হালকা হবে। (আরাফ ৯, মুমিনুন ১০৩)
১১. যারা আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে বাধা দেয়, সেই পথকে বাঁকা করে দিতে চায় এবং আখেরাত অস্বীকার করে। (হুদ ১৯-২২)
১২. অন্তরের নিফাকের কারণে ইবাদত করেও ক্ষতিগ্রস্ত। (হজ ১১)
১৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা। (যুমার ১৫)
১৪. ওজনে কম দেয়া। (রহমান ৯)
ইমাম ইবনে তাইমিয়া ২টি শব্দে ক্ষতিগ্রস্ততার মূল কারণ সামারাইজ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন- ২টি বিষয় মানুষকে সত্য বা হক গ্রহণ করতে বাধা দেয় যার ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের দলভুক্ত হয়। ১. শুহুবাত (সন্দেহ, সংশয়) ২. শাহাওয়াত (প্রবৃত্তি বা চাহিদা)। (মা’আরিফুল কুর’আন) উপরের পয়েন্টগুলো মোটাদাগে এই দুই ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়।
ক্ষতির বিপরীত হল সফলতা। ফালাহ অর্থ সফলতা। ধাতু হল ‘ফা-লাম-হা’। কুর’আনে ধাতুটি ২ টি রূপে (ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্য) ৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আবার নির্গত হয়েছে ‘ফালাহা ইয়াফলাহু’ থেকে যার মানে কোন বস্তুকে চিরে ফেলা, বিদীর্ণ করা। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে- ‘ইন্নাল হাদিদা বিল হাদিদি ইউফলাহু’, অর্থাৎ লোহাকে লোহার মাধ্যমেই কাটা যায়। আধুনিক আরবিতে কৃষককে বলা হয় ফাল্লাহ। কারণ, কৃষক হালের সূচালো মাথা দিয়ে জমির বক্ষকে বিদীর্ণ করে, চিরে ফেলে (কুরতুবি)। প্রকৃতপক্ষে হেদায়েত বিষয়টি আমাদের বক্ষে সুপ্ত অবস্থায় আছে, সেটিকে বিদীর্ণ করে বাইরে উন্মুক্ত করাটাই মূল সফলতা। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অর্থাৎ পরিশ্রম সফলতার মূলমন্ত্র। কল্যাণের জন্য কষ্ট করতে হবে। দৈনিক ৫ বার আমাদের কল্যাণের দিকে আহ্বান করা হয় ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’। এই কল্যাণের জন্য আল্লাহর রাস্তায় শ্রম দেয়ার কোন বিকল্প নেই কেননা ফালাহ বা কল্যাণ শব্দটির মধ্যে পরিশ্রম নিহিত। আর এজন্যই সূরা বালাদে বলা হয়েছে ‘আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি’। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামের শুয়ে শুয়ে সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। মানুষ কষ্ট করতে করতেই মৃত্যু ও তার রবের সাক্ষাতপ্রাপ্ত হবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিও নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে (বালাদ ৪)। তাই পরের আয়াতে মানুষের জন্য করণীয় কাজগুলো বিবৃত হয়েছে।
৩ নং আয়াতَ
ِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ
تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِকিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়।
ইল্লা শব্দ দ্বারা বাক্যকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তার মানে মেজরিটি ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকবে। স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম হবে। একই সুরে অন্যস্থানে এসেছে, “তারপর (এই সঙ্গে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে১৩ এবং যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়” (বালাদ ১৭)। “অনিবার্যভাবে আখেরাতে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে” (হুদ ২২-২৩)।
চাবি শব্দ: ঈমান, আমলে সালেহ, হক, সবর, উপদেশ (ওসিয়ত)
মূলশব্দ ঈমান যার ধাতু ‘আলিফ-মিম-নুন’ অর্থ- নিরাপত্তা দান করা, শান্তি, স্বীকৃতি ইত্যাদি। এই ধাতু নির্গত ক্রিয়াপদের পরে ‘লাম’ যুক্ত হলে তা স্বীকার করা অর্থ বুঝাবে। আর ‘বা’ যুক্ত হলে বিশ্বাস বা ইয়াক্বীন বুঝাবে। এর কর্তাবাচক শব্দ ৪ টি, যথা- আমান, আমিন, মুমিন, মামুন। মুমিন মানে বিশ্বাসী। আল্লাহ তায়ালার একটি নাম মুমিন। কুর’আনের একটি সূরাও আছে মুমিন (৪০ নং), বহুবচনে মুমিনুন (২৩ নং সূরা) নামেও সূরা আছে। আমানত শব্দটিও একই ধাতু থেকে আগত। তাই মুমিনের একটি ভিত্তিমূলক বৈশিষ্ট্য হল আমানতদারিতা। যে আমানত রক্ষা করে তাকে আমিন বলে। মুনাফিকের জন্য তাই আমানত রক্ষা করা সম্ভব নয় কারণ বিষয়টি তার ধাতে কিংবা জাতে নাই। ধাতুর অর্থ আমলে নিলে তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঈমান মানুষকে নিরাপত্তা দিচ্ছে সকল ধরণের ক্ষতি থেকে, শান্তি দিচ্ছে বৃদ্ধ বয়স বা সংকটের সময়ের দুর্ভোগ থেকে।
ঈমান ইসলামী নৈতিকতার প্রথম ও প্রাথমিক পর্যায় যার মাধ্যমে ইসলামী জীবনধারার পথচলা শুরু হয়। এর চুড়ান্ত মঞ্জিল হল ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া। স্বাভাবিক অর্থে, ঈমান মানে বিশ্বাস। সংজ্ঞা দিতে হলে বলতে হয়- যে বিষয়ে সরাসরি (ইন্দ্রিয়লব্ধ) জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাই বিশ্বাস।
বিশ্বাসের তিন অবস্থা –
* ইতিবাচক
* নেতিবাচক
* সন্দেহ
বিশ্বাসের অংশও তিনটি –
* অন্তরে অনুধাবন
* মৌখিক স্বীকৃতি
* কর্মে বহি:প্রকাশ
যিনি ঈমান আনেন অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করেন তাকে মুমিন বলে। মুমিন দুই ধরণের –
১. সাবিকুন (অগ্রগামী)/ মোকাররবুন (নিকটবর্তী)
২. আবরার (নেককার)/ আসহাবুল ইয়ামিন (ডান দলের লোক) [সূরা ওয়াকিয়া দ্রষ্টব্য]
ঈমান আনার পর একজন মুমিনের কী করণীয়?
— সংশয়ে লিপ্ত না হওয়া (হুজুরাত ১৫)
— ঈমানের উপর অবিচল থাকা (হামীম আস সাজদা ৩০)
বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় –
ক. মুমিন (বিশ্বাসী)
খ. কাফির (অবিশ্বাসী)
গ. মুনাফিক (সংশয়ী) [ সূরা বাকারা ১-১৪ আয়াত দ্রষ্টব্য]
মুমিনের অন্তরের (ক্বলব) অবস্থাও তিনটি –
১. ক্বলবে সহীহ
২. ক্বলবে সালিম; সুস্থ অন্তর (শুআরা ৮৯)
৩. ক্বলবে মুনিব; বিনীত অন্তর (ক্বাফ ৩৩)
প্রসঙ্গত: প্রশ্ন তুলতে পারেন ঈমান এনে কী লাভ? আসুন মুমিনদের ব্যপারে আল্লাহ তায়ালার কিছু ওয়াদা জেনে নিই-
১. আল্লাহ মুমিনদের পৃষ্ঠপোষক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (বাকারা ২৫৭)
২. পবিত্র জীবন দান করবেন। (নাহল ৯৭)
৩. মানুষের অন্তরে মুমিনের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করেদেন। (মরিয়ম ৯৬)
৪. দুনিয়াতে খিলাফত (শাসন ক্ষমতা) দান করবেন। (নূর ৫৫)
৫. ইহকাল ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (ইব্রাহিম ২৭)
৬. নেয়ামত ভরা জান্নাত দেবেন। (লুকমান ৮, কাহফ ১০৭)
৭. মুমিনদের বিজয়ী করেন। (ইমরান ১৩৯)
৮. মুমিনদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। (রুম ৪৭)
৯. এছাড়া রয়েছে প্রভূত সম্মান, ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (আনফাল ৪)
১০. এবং রয়েছে ব্যাপক অনুগ্রহ। (আহযাব ৪৭)
১১. কিয়ামত দিবসের অন্ধকারে তাদের সামনে ও ডানে নূর বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। (হাদীদ ১২)
আমল: আমল অর্থ কর্ম, উৎপাদন, পরিচালনা, অনুশীলন ইত্যাদি। ‘আইন-মিম-লাম ধাতুটি ৪টি রূপে ৩৬০ বার কুর’আনে বর্ণিত হয়েছে। তাহলে সেটাই কর্ম বলা হবে যা প্রোডাক্টিভ হবে, একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে এবং এর একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে বারবার করা। ইমাম তাইমিয়ার মতে, কর্ম তিন ধরণের। যথা- প্রথমত, সেই সকল কর্ম যা ভালো কিংবা মন্দ তা শরিয়াহ নাযিলের আগেও তেমনই ছিল। অর্থাৎ যেসব কর্ম যুক্তির বিচারেও ভাল-মন্দ যেমন ছিল, শরিয়াহর মানদণ্ডেও তেমনই। তার মানে আবার এই নয় যে, শরিয়াহ’র রায় দেয়ার পূর্বে সংঘটিত কোন ব্যক্তির খারাপ কাজের জন্য তাকে এখন শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেসব কর্ম শরিয়াহ প্রণেতার আদেশের মাধ্যমে ভালো কিংবা মন্দ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তৃতীয়ত, সেসব কর্ম যা শরিয়াহ প্রণেতা এজন্য আদেশ করেছেন যে তিনি দেখতে চান কে বা কারা তা যথাযথ কিংবা যথাসাধ্য মেনে চলছে। এক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ, কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটি বিবেচ্য নয়। যেমন- ইবরাহিম আ.কে পুত্র কুরবানির আদেশ করা (মাজমু ফাতওয়া ৮:৪২৮-৪৩৬)।
সালেহ: সালিহাত শব্দটি বহুবচন। এখানে বহুবচনের অর্থ হল নেক কাজ অসংখ্য। একটি, দুটিতে সীমাবদ্ধ নয়। এবং আমল শব্দের অনুশীলন অর্থ নিলে নেক আমলের স্পিরিট হল বারবার করা। একবচন সালিহুন। যে নেক আমল করে তাকে সালিহ/মুসলিহ বলে। শব্দটি ‘সালাহা’ ধাতু থেকে উদগত। এর অর্থ ব্যাপকতর। আরবি-ইংরেজি অভিধান থেকে সরাসরি তুলে দেয়া সমীচীন মনে করছি-
to be good, right , proper, in order, righteous, pious Godly. to be well, to be usable, practicable, suitable, appropriate. to be admissible, permissible. to be valid. to put in order, settle, adjust,make amends. to mend, improve, fix, repair. to make peace, become reconciled, make up. to poster peace (between), reconcile (among people). to make suitable, modify. To reform. to remove, remedy. to make arable, reclaim, cultivate. to further, promote, encourage. Bring good luck. To agree, accept, adopt (মিল্টন কোয়ান, ১৯৬১).
আমরা জানি ‘আমল’ (عمل) মানে- কর্ম ও আচরণ। তাহলে ‘আমলে সালেহ্’ মানে কী দাড়ায়? মূলত আমলে সালেহ্ মানে সেই সব কর্ম ও আচরণ যা সলাহা শব্দমূলের অর্থের মধ্যে এবং ‘সলাহা’ থেকে গঠিত শব্দসমূহের মর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে। উপরে বর্ণিত আভিধানিক অর্থের আলোকে আমরা বলতে পারি, ‘আমলে সালেহ্’ মানে- সেইসব কর্ম ও আচরণ, যা ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সৎ, সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ নির্দেশিত, সর্বজন স্বীকৃত ন্যায্য ও বাস্তব। আমলে সালেহ্ মানে- শান্তি, শান্তি স্থাপন, সমঝোতা স্থাপন, মিলে মিশে চলা, নিষ্পত্তি করে নেয়া। মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সমঝোতা করে চলা, সন্ধি স্থাপন করা। মীমাংসা করে নেয়া। সংযমশীল হওয়া। আমলে সালেহ্ মানে- যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও উপযুক্ততা অর্জন করা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের কাজ করা, নিজেকে যোগ্য, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বানানোর কাজ করা। ধারণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা অর্জন করা। আমলে সালেহ্ মানে সেইসব কাজ- যা উপকারী, সাহায্যকারী, কল্যাণকর, উন্নতিদানকারী; যা সুবিধাদানকারী, ফলদায়ক, লাভজনক।আমলে সালেহ্ অর্থ- সংস্কার, সংশোধন, পরিমার্জন, পুননির্মাণ, পুণর্বহাল, পুনর্মিলন, নিরাময়, খাদ পরিশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজ করা। আমলে সালেহ্ মানে- পরামর্শ করে কাজ করা, উপদেশ গ্রহণ করা, স্বীকৃত পন্থায় কাজ করা।আমলে সালেহ্ মানে- ভদ্র, সৌজন্য মূলক এবং সুন্দর ও চমৎকার আচরণ করা (আবদুস শহীদ নাসিম, ২০০৯)। ‘সলাহা’ ধাতু ৭ টি রূপে কুর’আনে ১৮০ বার বর্ণিত হয়েছে। উপর্যুক্ত অর্থগুলো আয়াতের ভাবের সাথে রিলেট করুন।
ইমাম ইবনে হাজর-এর মতে, ঈমানের শাখা সমূহ সম্প্রসারিত হয়েছে:
১. মানুষের অন্তরের আমলের মধ্যে (২২টি);
২. মানুষের যবানি (মৌখিক) আমলের মধ্যে (৭টি);
৩. মানুষের শারিরিক আমল বা বাস্তব কর্মের মধ্যে (৩৮টি)। মোট ৬৭টি
কুর’আনে ৭৭ বার ঈমান ও আমলে সালেহকে একত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমানভিত্তিক কিছু আমলে সালেহ’র তালিকা নিচে দেয়া হল:
♦অন্তরে উপলদ্ধিগত আমল
১. এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন। (বাকারা ২৮৫)
তার সাথে শরীক না করা। (মুমিনুন ৫৭)
২. মালাকদের (ফেরেশতা) উপর বিশ্বাস। (বাকারা ২৮৫)
তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বা ক্ষমতার অংশী মনে না করা। কাউকে শত্রু মনে না করা।
৩. আসমানি কিতাব সমূহের উপর, যা নবী (স:) ও পূর্ববর্তীদের উপর নাযিল হয়েছে। (বাকারা ২৮৫)
৪. রসুলদের (আলাইহিমুস সালাম) উপর বিশ্বাস। তাদের মধ্যে পার্থক্য না করা। (বাকারা ২৮৫)
তাদের প্রতি স্রষ্টার গুণাবলী বা অতিমানবিকতা আরোপ না করা। কারও প্রতি হিংসা, শত্রুতা বা অবজ্ঞা
পোষণ করা যাবে না।
৫. গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। (বাকারা ৩)
৬. পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন (বাকারা ৪)
আল্লাহর কাছেই ফিরে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করা। (বাকারা ২৮৬)
৭. আল্লাহর উপর সর্বদা নির্ভর করা। (আনফাল ২)
৮. সত্যকে মেনে নেয়ার মন গড়ে তোলা। (রাদ ১৯)
অর্থাৎ চোখ থাকতে অন্ধ না হওয়া।
৯. বিশ্বাসের পর সংশয়ে নিপতিত না হওয়া (হুজুরাত ১৫)। বিশ্বাসে অবিচল থাকা (হামীম আস সাজদা ৩০)
১০. আগামী দিনের(পরকালের) পাথেয় চিন্তা করা। (হাশর ১৮)
১১. আল্লাহ সমপর্কে বিশ্বাসের আরো কতিপয় দিক –
* আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের একমাত্র সার্বভৌম মালিক। বিধানদাতা।
* যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন। যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন।
* যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা – প্রভাব -প্রতিপত্তি কেড়ে নেন।
* যাবতীয় কল্যাণ তার হাতে (ইখতিয়ারে)।
* জীবিত থেকে মৃত বের করেন। আবার মৃত থেকে জীবিতকে বের করতে পারেন।
* যাকে ইচ্ছা বেহিসেবী রিযিক দান করেন। (ইমরান ২৬,২৭)
রিযিক আল্লাহর ইচ্ছায় বাড়ে -কমে। (বাকারা ২১২)
আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি পাখির মত রিযিক দেবেন।
* যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। (বাকারা ২৮৪)
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। তিনি ইচ্ছা করলে সব ধরণের গুণাহ ক্ষমা করতে পারেন। (যুমার ৫৩)
* ভালো -মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় সাধিত হয়। এখানে অন্য কোন শুভ/অশুভ শক্তি বা ব্যক্তির প্রভাব নেই। (মায়িদা ৪১, জিন ২১)
* আল্লাহ তায়ালাই শুধু গায়েব জানেন। আর কেউ গায়েব সমপর্কে বিন্দুবৎ কিছু জানে না। এমনকি রাসুলও (স:) জানতেন না। (যতটুকু আল্লাহ তাকে জানাতেন ততটুকু ব্যতীত) (বাকারা ৩৩, ফাতির ৩৮, সাবা ৩)
* সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি কাউকে পুত্র দেন, কাউকে কন্যা দেন, কাউকে উভয়ই দেন, কাউকে নি:সন্তান রাখেন। (শূরা ৪৯,৫০)
* রোগমুক্তিকারীও একমাত্র আল্লাহ। তার কাছেই চাইতে হবে। (শোয়ারা ৮০)
* প্রার্থনা সরাসরি (মাঝে কোন মাধ্যম ছাড়া) আল্লাহর কাছেই করতে হবে। (আনআম ৪১-৪২, আরাফ ২৯)
* সকল সুন্দর নাম আল্লাহর জন্যই। (হাশর ২৮)
* কুরআনে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপক যে উপমা (যেমন আল্লাহর হাত,পা, কান ইত্যাদি) দেয়া আছে তা রূপক অর্থে আল্লাহর ক্ষমতা কিংবা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে ভাবতে হবে। কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সমান হতে পারে না।
* আল্লাহ কারও ইবাদত বা সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। (ইখলাস ২, ফাতির ১৫)
♦মুয়ামেলাত বা ব্যবহারিক আমল
১. অবিশ্বাসী ও আহলে কিতাবদের* বন্ধু বানানো যাবে না। (ইমরান ২৮)
২. মুমিনেরা পরস্পর ভাই। তারা নিজেদের সংশোধন করে। (হুজুরাত ১০)
৩. মুমিন নারী ও পুরুষ সৎকাজে পরস্পরের সহযোগী। (তাওবা ৭১)
৪. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। (রাদ ১৯)
৫. সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। (রাদ১৯)
৬. অর্থহীন বিষয়ে বিমুখ থাকে। অযথা বিষয় থেকে সরে আসে। (মুমিনুন ৩, ফুরকান ৬৫)
৭. আব্রুর হেফাজত করে। (মুমিনুন ৫)
৮. যমীনে বিনম্রভাবে বিচরণ করে। (ফুরকান ৬৩)
৯. মূর্খদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে শান্তি কামনা করে। (ফুরকান ৬৪,ক্বাছাছ ৫৫)
১০. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (ফুরকান ৬৫)
১১. সন্তান -স্ত্রী -পরিবারের প্রতি দয়ার্দ্র ও দুআ করে। (ফুরকান ৭৪)
১২. সৎ কাজের আদেশ /উপদেশ /উৎসাহ /অনুরোধ করে। (আসর ৩, ইমরান ১০৪,১১০)
১৩. অসৎ কাজের নিষেধ /প্রতিরোধ /নিরুৎসাহিত করে। (ইমরান ১০৪,১১০)
১৪. পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়। (আসর ৪)
১৫. বাজে কথা কানে নেয় না। (ক্বাছাছ ৫৫)
১৬. সত্য ও সঠিক কথা বলে। (আহযাব ৭০)
১৭. সত্যপন্থী লোকের সঙ্গী হয়। (তাওবা ১১৯)
১৮. পরস্পর গোপন কথা বললে আল্লাহ ও রাসুলের (স:) নাফরমানির কথা নয় বরং তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার কথা বলে। (মুজাদালাহ ৯)
১৯. অতি ধারণা(কুধারণা)পোষণ করে না। গীবত করে না। কারও গোপনীয় বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করে না। (হুজুরাত ১২)
২০. অনুমতি ছাড়া কারও গৃহ/ঘরে প্রবেশ করে না। (নুর ২৭)
২১. অন্যের আবাসে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে। (নুর ২৭)
২২. মুমিনেরা পরস্পরের প্রতি কোমল, নম্র ও বিনয়ী কিন্তু কাফিরদের প্রতি আপোষহীন। (মায়িদা ৫৪)
♦আনুগত্য ও ইবাদত কেন্দ্রিক আমল
১. পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে। (বাকারা ২০৮)
২. সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চায়। (বাকারা ১৫১)
৩. নিজে যা করে না তা বলে বেড়ায় না। (সফ ২)
৪. আল্লাহ তায়ালার সামনে রুকু -সিজদা ও যথাযথ আনুগত্য করে। এবং সৎকর্ম করে। (হাজ্জ ৭৭)
৫. মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারি (ভাগ্য গণনা) ইত্যাদি অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। (মায়িদা ৯০)
৬. আল্লাহর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ থাকে। পবিত্র রিযিক থেকে আহার করে। (বাকারা১৭২)
৭. আল্লাহর নামেই কুরবানি (পশু জবাই) করে ও গোশত খায়। (আনয়াম ১১৮)
৮. বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে (তাওবা করে)। (তাহরীম ৮, নূর ৩১)
৯. দৃষ্টিকে সংবরণ করে। সাজসজ্জা করে বেড়ায় না। (নূর ৩০)
১০. আল্লাহ, রাসূল ও দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করে। (নিসা ৫৯)
আল্লাহর নির্দেশ শোনা মাত্র কাল বিলম্ব না করে মেনে নেয় (বাকারা ২৮৫)
সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। (তাওবা ৭২)
১১. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে (মায়িদা ৩৫)
১২. আল্লাহ ও রাসূলের সামনে(সিদ্ধান্তের বাইরে) অগ্রসর হয় না। (হুজুরাত ১)
১৩. মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করে না। (ইমরান ১০২)
১৪. ভালো কাজ ও প্রচেষ্টা দ্বারা মন্দকে দূর করার চেষ্টা করে। (ক্বাছাছ ৫৩)
১৫. সালাতে বিনয়াবনত ও যত্নবান হয়। (মুমিনুন ২,৯)
সালাতের দিকে ডাকলে সে দিকে ধাবিত হয়। (জুমুয়া ৯)
সিজদা ও সালাতে দাঁড়িয়ে রাত যাপন করে। (ফুরকান ৬৩)
১৬. নেকীর কাজে তৎপর ও অগ্রণী হয়। (মুমিনুন ৬১)
১৭. মুমিনের সামনে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না। অর্থাৎ সাড়া দেয়, মেনে নেয় ও বাস্তবায়ন করে।
১৮. মুক্তহস্তে দান করে। (মুমিনুন ৬০)
আল্লাহর পথে ব্যয় করে। (আনফাল ৪)
১৯. সাওম পালন করে। আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা মেনে চলে। (তাওবা ১১২)
২০. আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেয়। (হাদীদ ১১)
♦সামষ্টিক/সামাজিক বিষয়ে আমলে সালেহ
১. সালাত (ব্যক্তিগত, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে) প্রতিষ্ঠিত করবে। (বাকারা ৩, আনফাল ৩, তাওবা ৭২, রাদ ২৩, হাজ্জ ৩৫)
২. যাকাত (যথাযথ আদায় ও খাত অনুসারে ব্যয়) নিশ্চিত করা। (মুমিনুন ৪)
৩. (ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত) কাউকে হত্যা করে না। (নিসা ৩০, ফুরকান ৬৮)
৪. ব্যভিচার করে না। (ফুরকান ৬৮)
৫. পারস্পরিক বিরোধে রাসূল (স)কে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়। (নিসা ৬৫)
৬. আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফয়সালার (আইন -বিচার) জন্য ডাকলে বলে শুনলাম ও মেনে নিলাম। (নূর ৫১)
৭. জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (মায়িদা ৩৫, হুজুরাত ১৫,সফ ৯)
৮. আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়। (মুহাম্মদ ৭, সফ ১৪)
৯. বাতিলের মোকাবেলায় দৃঢ় ও অনমনীয় হয়। এবং আল্লাহর পথে সার্বক্ষণিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে।
১০. দ্বীন রক্ষার জন্য শপথবদ্ধ হয়। (ফাতহ ১৮)
১১. সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্তভাবে দাড়িয়ে যায়। (নিসা ১৩৫)
১২. ফিতনা – ফ্যাসাদ নির্মূল ও দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য খালেস না হওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। (আনফাল ৩৯)
♦আবেগ- অনুভূতি ও ভালোবাসা বিষয়ক আমলে সালেহ
১. শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চায়। (ফাতিহা ৪, বাকারা ২৮৫)
২. আল্লাহর স্মরণে হৃদয় কেঁপে উঠে। (আনফাল ২, হাজ্জ ৩৫)
৩. আল্লাহর আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাস স্থাপন করে। (আনফাল ২, ক্বাছাছ ৫৩)
৪. আল্লাহ তায়ালাকে সর্বাধিক ও দৃঢ়ভাবে ভালোবাসে। (বাকারা ১৪৫)
৫. আল্লাহর প্রসংশা করে। (তাওবা ১১২)
৬. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করে। (রাদ ১৯)
৭. আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে। সর্বদা ভীত থাকে। (রাদ ২০, তাওবা ১১৯, ইমরান ১০২, মায়িদা ৫৩, হাশর ১৮, মুমিনুন ৫৭)
৮. বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করে। (রাদ ২১, হাজ্জ ৩৫, ক্বাছাছ ৫৩)
৯. আল্লাহকে যথেষ্ট ও সর্বোত্তম অভিভাবক মনে করে। (ইমরান ১৭৩)
১০. বাতিলের ভয়ে ভীত, চিন্তিত ও হতাশ হয় না। (ইমরান ১৩৯)
১১. আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাড়িয়ে যায়। (নিসা ১৩৫)
♦পারস্পরিক লেন -দেন ও চুক্তি সংক্রান্ত আমলে সালেহ
১. আমানত সংরক্ষণ করে। (মুমিনুন ৭, আনফাল ২৭)
২. অপব্যয় করে না। কার্পণ্যও করে না। (ইসরা ২৩, ফুরকান ৬৭)
৩. অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে না। (নিসা ২৯)
৪. চুক্তির মাধ্যমে লেন -দেন করে। (নিসা ৩০)
৫. নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ আদানকালে লিখিত চুক্তি করে। (বাকারা ২৮২)
৬. কৃত চুক্তি পূরণ করে। (মায়িদা ১)
৭. সুদ পরিহার করে (বাকারা ২৮২)
৮. আল্লাহর স্মরণের দিকে আহবান করলে (সালাতের আযান হলে) ব্যবসা, বেচা-কেনা স্থগিত রাখে। (জুমুয়া ৯)
৯. পরিমাপে (ওজন) কম দেয় না। (রাহমান ৯)
পরবর্তী যে দুটি কাজের কথা বলা হয়েছে- হক ও সবরের উপদেশ সেটিও কিন্তু আমলে সালেহ’র অন্তর্ভুক্ত। এটি বললে অত্যুক্তি হবে না, এখানে মৌলিক নির্দেশনা দুটি হল ঈমান ও আমলে সালেহ। আর আমলে সালেহ’র উদাহরণ হিসেবে হক ও সবরের উপদেশ প্রদানের উল্লেখ করা হয়েছে। ‘সলাহা’ ধাতুর একটি রূপ ‘ইসলাহ’ যার অর্থ খেয়াল করলেও দেখা যায় to correct, reconcile বা সংশোধন করা। “মু’মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও” (হুজুরাত ১০)।
তাওয়াসসু/তাওয়াসসি: মূলশব্দ ‘ওয়াসিয়্যা’। বুৎপত্তিগত অর্থ কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা (আনকাবুত ৪, পরস্পরকে উপদেশ দেয়া (বালাদ ১৭, আসর ৩), আদেশ করা/জোর নির্দেশ দেয়া (নিসা ১১), আবেগীয় উৎসাহ দেয়া (emotional motivation)।’ওয়া-সোয়াদ-ইয়া’ ধাতুটি ৭ টি রূপে ৩২ বার কুর’আনে এসেছে। ওসিয়ত বলতে আমরা বুঝি, মৃত্যুর আগে কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার প্রিয়জনদের (beloved) দেয়া উপদেশ, পরামর্শ, কর্মতালিকা, সম্পত্তি প্রদানের অনুরোধ ইত্যাদি। ওসিয়তের মেজাজের দিকে মনোযোগ দিলে আমরা উপদেশের বৈশিষ্ট্য পাই- আপনি কোমলত্ব বিশিষ্ট কোমল মনের, সামাজিক মানুষ। আপনি অন্যকে উপদেশ দেবেন কোমল ভাষায়, কোমল-ভালোবাসাপূর্ণ (loving) হৃদয়ে, যাকে উপদেশ দেবেন তাকে নিজের প্রিয়জন ভাববেন, তাকে মূল্যবান পরামর্শ দেবেন, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ, উপদেশ দেয়াকে জরুরি মনে করবেন, এতে উভয়পক্ষের কল্যাণ নিহিত আছে। বুৎপত্তিগত অর্থ আমলে নিলে দাঁড়ায়-
১। যার ওপর আপনার কর্তৃত্ব নাই (যেমন- সমাজের অন্য মানুষ), তাকে উপদেশ দিন। উৎসাহিত করুন।
২। যে আপনার নিয়ন্ত্রিত, অনুগত (যেমন- পরিবার, ক্রীতদাস, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জনগণ) তাকে আদেশ দিন।
৩। উৎসাহিত কিংবা অনুগত হলে দায়িত্ব অর্পণ করুন।
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে- জ্ঞানের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়- ১. জাহেল বা মূর্খ ২. তালবে ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারী ৩. আলিম বা জ্ঞানী। মানুষের কাছে হকের উপদেশ পৌঁছে দেয়ার ৩ টি পদ্ধতি রিলেট করা যায়- যে মূর্খ তার সাথে বিতর্কে যাবেন না, উত্তম নসিহত করবেন। না বুঝতে চাইলে সালাম বা শান্তি কামনা করে চলে আসবেন (ফুরকান ৬৪)। যে তালবে ইলম তাকে হিকমত শিক্ষা দিন, হিকমতের সাথে উপদেশ তুলে ধরুন। যিনি আলিম তাঁর সাথে হকের উপদেশ তুলে ধরুন, প্রয়োজনে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন (নাহল ১২৫)। তাহলে ওয়াতাওয়াসাও বিল হাক্কি… এর অর্থ কেবল উপদেশ করব না, এতে শব্দের গভীরতা ও মাহাত্ম্য, প্রয়োগ সংকীর্ণ হয়ে যায়।
হক: হক শব্দটি ‘হা-ক্বফ-ক্বফ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। উক্ত ধাতুটি ৭টি রূপে ২৮৭ বার কুর’আনে এসেছে। হক শব্দের অর্থ সত্য, সঠিক, অধিকার, সর্বোত্তম, যথাপোযুক্ত, প্রয়োজনীয়, আইনত সিদ্ধ, পরস্পর মিলে যাওয়া, জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
আসলে হক বা সত্য কী? আমরা জানি সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সত্য-মিথ্যা বরাবর একটা বাইনারি ধারণা। যা মিথ্যার বিপরীত তাই তো সত্য। তাহলে মিথ্যা কী? যা অশুদ্ধ, কৃত্রিম, অপ্রতিষ্ঠিত তা পুরো মিথ্যা। সত্য-মিথ্যার ধারণা মানবেতিহাসের সমবয়সী কিংবা তার চেয়েও ঢের বেশি। দার্শনিকদের মতে,
“মানুষের বিবেক আল্লাহ এবং সকল বাস্তবতা সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, যেমন এটি ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম। ওহি দরকার আমজনতার জন্য যাদের বিবেক, আবেগ দ্বারা অবদমিত। তাদের জন্যই যুগে যুগে নবি পাঠানো হয়েছে, তাদের ভাষাতেই পাঠানো হয়েছে যেন তারা এর দৃষ্টান্ত ও রূপক কথাগুলো বুঝতে পারে। যখন পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এবং অলংকারহীন ভাষায় উপস্থাপিত হলে, তাদের তত্ত্বগুলো দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে খুব বেশি আলাদা হবে না যা তারা বিবেকের যুক্তি দিয়ে আবিষ্কার করেছে। সত্য সব একই রকম, তা প্লেটো-এরিস্টোটল বলুক আর মুসা-মুহাম্মদই বলুক। সত্য জানার অসাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও একজন নবিকে অসম্ভব শক্তিশালী কল্পনাশক্তি দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার দরুন তিনি ন্যায়ানুগ যুক্তিসমূহকে ভৌতজ্ঞানের আকারে উপস্থাপন করতে পারেন এবং অলৌকিক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন। যা হোক, এই ক্ষমতাগুলো নবি ছাড়াও অনেকের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে বিরাজমান থাকে” (আনসারি, ২০০৯; অনুবাদ: বাপ্পা আজিজুল) হক বা সত্য সম্পর্কিত দার্শনিকদের এই ভ্রান্ত ধারণা ইমাম গাজালি ও ইবনে তাইমিয়া সমালোচনাপূর্বক বাতিল করেছেন।
কুর’আনে হক শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-
১. অকাট্য সত্য: আল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ, নবি-রাসূল, কিতাব-কুর’আন, দ্বীন ইসলাম, আল্লাহর আদেশ ইত্যাদি বুঝাতে। (ইসরা ৮১, সফ ৯, তাওবা ৩৩, ফাতহ ২৮)। আল-হক্ক, আল্লাহ তায়ালার একটি সিফাত।
২. অবশ্যম্ভাবী সত্য: কিয়ামত, আখিরাত বুঝাতে। (হাক্কাহ ১-৩)
৩. অধিকার অর্থে, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। (যারিয়াত ১৯)
আলোচ্য আয়াতে হকের উপদেশ বলতে বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন মত দিয়েছেন-
যামাখশারী বলেছেন: তাওহীদ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা, দুনিয়াবি উচ্চাভিলাষ থেকে দূরে থাকা ও পরকালের দিকে ঝুঁকে থাকার উপদেশ দেয়া। ইমাম শাওকানীর মতে, তারা পরস্পরকে সেই সত্যের উপদেশ দেয় যা পালন, প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের দাবি রাখে। কাতাদা মনে করেন, এর অর্থ কুর’আন। অর্থাৎ পরস্পরকে কুর’আনের দিকে কুর’আন দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে। ইবনে কাসির করেছেন, সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ। ইমাম শানক্বীতি বলেছেন, আমলে সালেহ সম্পাদনের পর সেই সত্যটি অন্যের কাছে প্রকাশ করা। ইমাম ফারাহি মনে করেন, হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের সংরক্ষণ ও পরস্পরকে সেই সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া।
তাহলে দেখা যাচ্ছে, হক একটি বর্ণালীর মতো যার একপাশে ছোট ছোট হক্কুল ইবাদ (পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, আত্মীয়ের হক)থেকে শুরু করে পুরো ইসলাম, তাওহীদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা, কিয়ামত-আখিরাত-আল্লাহ তায়ালার দিদার সব অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হকের উপদেশের হক আদায় করতে চাইলে কোনটাকে বাদ দেয়া, মাইনর ভাবা যাবে না। আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার বৃহৎ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে অনেকসময় এসব হককে অগ্রাধিকার দেই না, যা মোটেও কাম্য নয়। বর্তমান সময়কে বলা হয় উত্তর-সত্য কাল (post truth era)। ২০১৬ সালে আসলে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে অবলীলায় যে মিথ্যা ভাষণ দেন, সেই সময়কে উত্তর-সত্য যুগের সূচনা ধরে শব্দটি প্রচলিত করেছে অক্সফোর্ড ডিকশনারি। এখন সমাজে, রাষ্ট্রে কিংবা বৈশ্বিকভাবে সত্যের কোন লেশ নেই। মিথ্যাই সমাজে অলংকৃত, চমৎকৃত, আধিক্য, প্রতিষ্ঠিত। এই ফ্যাসিবাদী সময় ও সমাজে হকের উপদেশ দিতে যাওয়া নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এতে বৈষয়িক নানাবিধ ক্ষতি হওয়ার শংকা প্রবল। তাই আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরবর্তীতে সবরের ওয়াজ করেছেন।
আরবি ‘সবর’ শব্দটি ‘সব্বার’ ধাতুমূল থেকে উদগত। সব্বার মরুভূমিতে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা কষ্টসহিষ্ণু এলোভেরা জাতীয় উদ্ভিদ যার ঔষধিগুণ বিদিত। এই উদ্ভিদের বাহ্যিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সবরের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।
সবর অর্থ ধৈর্য ধারণ করা। বলতে গেলে ধৈর্যের চেয়ে বেশি। ধৈর্যের সীমা আছে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সবরের সীমা নাই। ধৈর্য্য যেখানে শেষ সবর সেখান থেকে শুরু। সবরের চ্যুতি ইমানের বিপরীত। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ শব্দের মেজাজের মধ্যে হামদ, শোকর ও সবর নিয়োজিত আছে। কুর’আনে সবরে জামিল বা উত্তম ধৈর্য ধারণের কথা বলা হয়েছে। কুর’আনে প্রায় ৯০ বার ‘সবর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সবর ঈমানের একটি শাখা আবার কোথাও অর্ধেক বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানদারের গুণাবলির মধ্যে যেমন সবর রয়েছে তেমনি অন্যের প্রতি সবরের উপদেশ দেয়ার তাগিদও রয়েছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অন্যতম উপায় হিসেবে সালাতের সাথে সবরের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। শত্রুকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে পেতে চাইলেও সবর জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, মুমিনের পুরো জীবনই সবরের জিন্দেগি। কারণ তাঁর ঈপ্সিত পুরস্কার দুনিয়ায় নয়, আখিরাতে। সবর মানুষকে সফল করে। সবর মানুষকে সম্মানিতও করে। প্রসঙ্গত, ‘সবুরে মেওয়া ফলে’ প্রবচনটি শ্লেষাত্মক, যেমন ‘ভেস্তে যাওয়া’, ‘অজুহাত’ ইত্যাদি শব্দগুলো মুসলিমদের বিশ্বাস ও রিচুয়ালকে কটাক্ষ করে তৈরি হয়েছে।
আবুল আ’লার মতে, সবরের অর্থ হল-
১. তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা।
২. তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া।
৩. বাধা-বিপত্তির বীরোচিত মোকাবেলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখকষ্ট বরদাশত করা।
৪. দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়া।
৫. সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা।
তারিক রমাদান মনে করেন, সবর সম্পর্কে আমাদের একটা ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা এর অনুবাদ করি ধৈর্য। অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয় বসে থাকা, কিংবা সহ্য করা। কিন্তু এর নাম সবর নয়। সবর অর্থ নিরেট ধৈর্য নয়, সবর অর্থ অধ্যবসায়। অর্থাৎ আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। সবর অর্থ সক্রিয় ধৈর্য। অর্থাৎ আপনাকে একই সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সবর প্যাসিভ নয়, একটিভ। সবর অর্থ অন্যায়কে হজম করা নয়, বরং ধৈর্য সহকারে অন্যায় প্রতিরোধে কাজ করা। সক্রিয় ধৈর্য মানে সংগ্রামে আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল করা, ভরসা করা।
সবরের দিক:
১. আল্লাহর পরীক্ষায় সবর করা
২. ফল লাভের জন্য তাড়াহুড়া না করা
৩. ব্যক্তিগত মোয়ামেলাতে ধৈর্য্য ধারণ করা।
৪. নিজের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করা
ইবনে তাইমিয়া বলেন, সবর ৩ ধরণের-
১। অনৈচ্ছিক ঘটনার প্রেক্ষিতে যেখানে ব্যক্তির সবর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। যেমন- ইউসুফ আ. ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে দেয়ার পর ঘটেছিল।
২। ঐচ্ছিক বিষয়ে যেখানে ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- জুলেখার প্রলোভনে ইউসুফ আ. সবর করেছেন। এখানে তাঁর ইচ্ছা ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তিনি নিবৃত্ত থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। তাঁর এই সবর পূর্বের সবরের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।
৩। নেক আমলের মাধ্যমে সবর করা। এটি সর্বোত্তম সবর।
ইবনুল কাইয়্যিম সবরকারীর ৫ টি স্তরের কথা বলেছেন-
১. সাবির হল সাধারণ ও পরিপূর্ণ সবরকারী।
২। মুস্তাবির, যিনি উত্তম সবরের চেষ্টা করেন।
৩. মুতাসাব্বির, যিনি সাধনা করে সবর করেন।
৪. সবুর, অন্যদের তুলনায় যার সবর অত্যধিক।
৫. সব্বার, সর্বোচ্চ সবরকারী।
সবরের ৩ যাত্রা-
১. সবরে বিল্লাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে)
২. সবরে লিল্লাহ (আল্লাহর জন্য)
৩. সবরে মা’আল্লাহ (আল্লাহর সাথে)
সবরে বিল্লাহ মানে আমার সবর আল্লাহর দেয়া। আমার কোন ক্রেডিট নাই। সবরের জন্য তাই তাঁর কাছে দু’আ করতে হবে নিজেকে সঁপে দিয়ে। সবরে লিল্লাহ হল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের জন্য সবর করা। সবরে মা’আল্লাহ অর্থ আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয় ও পথে চলা, সেগুলো সংরক্ষণ করা, প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা, নফসকে সেসব বিষয়ের সাথে জুড়ে দেয়া। এটি সবরের চূড়ান্ত মঞ্জিল।
সবর পালনে ৪ টি উপদেশ-
১. লা তাহযান, হতাশ না হওয়া। অতীতের বিষয়ে দুশ্চিন্তা না করা।
২. লা তাখাফ, ভয় না করা। ভবিষ্যতের বিষয়ে ভীত না হওয়া।
৩. লা তাগদাব, রাগ করবেন না। বর্তমানের কোন বিষয়ে সবর করা।
৪. লা তাসখাব, আল্লাহ”র ফয়সালায় অসন্তুষ্ট না হওয়া। তাকদিরকে মেনে নেয়া।
সবরই কি শেষ? না। সবর হল মাইল্ড ফর্ম। সবরের চেয়েও শক্ত পদক্ষেপের আদেশ আছে। “হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে”। (৩:২০০)
এখানে দেখা যাচ্ছে, সবর হল ফার্স্ট স্টেপ। ২য় স্টেপ (মডারেট) ‘মুসাবারা’ মানে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়া। এরপর চূড়ান্ত ধাপ (সিভিয়ার) হল ‘মুরাবাতা’ অর্থ প্রাণপণে লেগে থাকা। আবার অনেকের মতে উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় মিলেই সবর। আল্লাহু আ’লাম। আমাদের অস্থির চিত্তকে থির করতে এবং সবরের অনুশীলনের জন্য আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি আমার মনে হয় শিথিলায়ন ব্যায়াম, মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন, রাগ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করা ফলপ্রদ হতে পারে।
কুর’আন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হল: নাজম-আল-কুর’আন। অর্থাৎ কুর’আনের প্রতি সূরা একে অপরের সাথে, প্রতিটি আয়াত একে অপরের সাথে সম্পর্কিত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করা। সূরা আসরের ৩ টি আয়াতেত শব্দগুলোর ধাতুভিত্তিক অর্থ ও প্রয়োগ জানার পর আমাদের প্রতিটি আয়াত ও শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরম্পরা বুঝতে আশা করি সুবিধা হয়েছে। এখন দেখুন- ১ম শব্দ আসরের সাথে শেষ শব্দ সবরের কত সম্পর্ক ও মিল! সময়ের কসম মানুষ সবরে অভ্যস্ত নয়, মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আশু ফললাভের জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে। মানুষ বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। দু:খ-কষ্ট, প্রয়োজনের সময় সবর করে না, বিধায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঈমান আনার সাথে সাথে সবরের পরীক্ষা শুরু হয়, আমলে সালেহ করতে গিয়ে সবরের পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করতে হয়। আমলে সালেহ’র যে পুরস্কার বা বিনিময় তাও নগদ নয়, মৃত্যুর পরের জীবনে। তাই সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর ওয়াদা পূরণের জন্য সবর করতে হয়।
শিক্ষা:
১. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও নামে (বাপ-দাদা, সূর্য-চন্দ্র, দেব-দেবী, খাবার দ্রব্যাদি ইত্যাদি) কসম করা যাবে না। ইবনু উমর (রা.) সূত্রে নবি সা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের কসম করতে হয় তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে কসম করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে কসম করো না। (বুখারি ৩৮৩৬)
কসম বা শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। “কোন কিছুর ব্যাপারে যদি শপথ কর আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফ্ফারা আদায় করে তাত্থেকে উত্তমটি গ্রহণ কর”। (বুখারি ৬৬২২, ৬৭২২; মুসলিম ১৬৫২)
২. সময়কে গালি দেয়া যাবে না। এই বছর খারাপ কিংবা যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ অথবা খারাপ জামানা ইত্যাদি বলা যাবে না। لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهرতোমরা যুগকে গালি দিও না। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই যুগ। (মুসলিম ২২৪৬)
৩. সময় বা যুগের ইতিহাসকে বিকৃত করা যাবে না। ভোলা যাবে না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর দিনগুলোকে স্মরণ করতে হবে।
৪. সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সময় ব্যবস্থাপনা শিখতে হবে। সময়কে উৎপাদনশীল করতে হবে।
৫. শিরকমুক্ত ঈমান এবং বিদাত, অহংকার ও রিয়ামুক্ত আমলে সালেহ সম্পাদন করতে হবে।
৬. হক ও সবরের আদেশ বা ওসিয়ত/পরামর্শ শুধু অন্যকে দিলে হবে না, আগে নিজে পালন করতে হবে। কেননা, “তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী” (আন’আম ১৬৩)। এবং “তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়” (সফ ৩)।
৭. হকের ওসিয়ত একটা বর্ণালী (Spectrum)। আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার বা সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ও ব্যক্তিগতভাবে অন্যের হক আদায় করা সবই এর অন্তর্গত।
৮. মুমিনের আল্লাহর দিকে যাত্রার শুরু হল ঈমান দিয়ে এরপর তাকে ইস্তেকামাত বা অবিচল থাকতে হবে। আমলে সালেহ পালনের মাধ্যমে ইয়াক্বীন অর্জন করতে হবে। হকের আদেশ দিতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি আসবে,তাতে ‘সব্বার’ বা সর্বোচ্চ সবরকারী হতে হবে এবং মুরাবাতা অর্জন করতে হবে।
ইসলামের আলোকে সময় ব্যবস্থাপনা (Time management)
পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদী সভ্যতা আমাদের শেখাতে চায় Time is money. কিন্তু সময় কেবল টাকা নয় কিংবা টাকার পেছনে ছোটা নয়। সময়ের অসংখ্য দিকের (dimension) এর মধ্যে এটি একটি হতে পারে। সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত। এই নেয়ামতের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তাহলে তিনি সময়ের বরকত দান করবেন (ইবরাহিম ৭)। সময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ৩ টি ধাপ বা পদ্ধতির যথার্থ সমন্বয় দরকার। যথা-
১. পরিকল্পনা (Planning)
২. পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিং (monitoring)
৩. যাচাই (Evaluation)
পরিকল্পনা: প্রতিটি কাজের জন্য লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থাকে। যেমন- ফেরেশতাদের মজলিশে আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা জানিয়ে বলেছিলেন, “আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে চাই” (বাকারা ৩০)। আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্যহীন কোন কিছু সৃষ্টি করেন না(ইমরান ১৯১)। তিনি আরও বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী” (ইমরান ৫৪, আনফাল ৩০)। সুতরাং একজন মুমিনের সময় বা দিন উদ্দেশ্যহীন, বেহুদা এবং পরিকল্পনাহীন হতে পারে না। উত্তমভাবে পরিকল্পনা করে দিন শুরু করতে হবে। সেটি আগের রাতে কিংবা ফজরের পরে দিনের শুরুতে হতে পারে।
একজন মুমিন দিনে ৪ ধরণের করণীয় কাজ (to do) করতে পারে। ইসলাম কেবল নেতিবাচক, অশ্লীল, প্রতারণামূলক কাজকে হারামই ঘোষণা করেনি, অযথা (Unproductive) কাজগুলোকেও (not to do) নিরুৎসাহিত করেছে। করণীয় কাজগুলো হল-
১. নিয়মিত কার্যাদি (Regular activities), খাওয়া-দাওয়া, গোসল, দাঁতব্রাশ, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি জৈবিক কাজ সম্পাদন করা।
২. প্রয়োজনীয় কার্যাবলী (Necessary activities) পড়াশোনা, জীবিকা, সন্তান পরিপালন, কারও সাথে সাক্ষাত, ব্যাংকে যাওয়া, রোগীকে ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি
৩. বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড (Pleasurable activities); খেলাধুলা, ব্যায়াম, বাগান করা, পশু-পাখি পোষা ইত্যাদি হালাল বিনোদনমূলক কাজ।
৪. আধ্যাত্মিক/সামাজিক কার্যক্রম (Spiritual & social activities); ৫ ওয়াক্ত নামাজ, রোযা, ঈমানের ভিত্তিতে যেকোন আমলে সালেহ, কুর’আন তিলাওয়াত, যিকির, সদাকা ইত্যাদি।
দৈনিক কাজের পরিকল্পনায় এইসব কর্মকাণ্ড একজন মুমিনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। মুমিনের দৈনিক শিডিউল হবে ৫ ওয়াক্ত জামায়াতের নামাজের ভিত্তিতে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভ হতে পারে। কোন ধরণের কাজই বাদ দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এইকাজগুলো মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে সুস্থ রাখে। স্বাস্থ্য আল্লাহর দেয়া আমানত ও নেয়ামত। সুতরাং সেটির সংরক্ষণও ইবাদত। ইবাদাতের ক্ষেত্রের আল্লাহর পছন্দের নীতি হল: “যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়” (বুখারি ১১৩২)। আল্লাহ তায়ালা দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি (হজ ৭৮)। কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি (বাকারা ২৮৬)। দ্বীন পালনে জোরাজুরি নেই (বাকারা ২৫৬)। আল্লাহ চান কঠিন নয় সহজ করতে (বাকারা ১৮৫)। আপনার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ৩ ধরণের হবে।
১. দীর্ঘমেয়াদী (২০-৩০ বছর ব্যাপী)
২. স্বল্পমেয়াদী (৩-৫ বছরের)
৩. দৈনিক (Daily)
তিন ধরণের কাজের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা SMART স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করতে পারি।
S: Specific-
M: Measurable
A: Achieveable
R: Relevent/Repeatable
T: Time limiting
অর্থাৎ আপনার দিন ও কাজের পরিকল্পনা হবে গোছানো ও সুনির্দিষ্ট, খুব বেশি বা বড় কিছু নয় ছোট ছোট টার্গেট বা কাজ যা সহজেই বাস্তবায়ন সম্ভব। কাজটি হিসাবযোগ্য কিংবা মূল্যায়ন করা যায় এমন। মুমিন অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে (মুমিনুন ৩)। আপনার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটি হাসিল করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সময় গেলে সাধন হয় না একটি প্রবাদ আছে। তেমনিভাবে আল্লাহও বলেছেন, “প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়” (ইউনুস ৪৯)। সময়কে ভাগ করে নেয়ার সুন্নাহ আমরা হাদিস থেকে পাই। ইবরাহিম আ. এর সহিফায় কী ছিল? আবু যার গিফারি রা. এর এমন প্রশ্নের জবাবে রাসুলুল্লাহ সা. জানান-
“জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য উচিত কিছুক্ষণের জন্যও সে যেন জ্ঞানশুন্য না হয়। এবং আপন সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেয়। প্রথম অংশ আল্লাহর ইবাদতে কাটাবে। দ্বিতীয় অংশ ভালো-মন্দ কৃতকর্মের হিসাব নিকাশে কাটাবে। তৃতীয় অংশ হালাল উপার্জন করবে ও ব্যয় করবে। বুদ্ধিমানের ইহাও কর্তব্য যে, সে যেন আপন সময়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, আত্মার উন্নতি সাধনে চিন্তাশীল হয়। অনর্থক কথাবার্তা হতে জবানকে হেফাজত করে। যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার হিসাব নিতে থাকবে তার মুখে অনর্থক কথা আর আসিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি তিন কাজে সফর করতে পারে। পরকালের ধন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে, কিছুটা রোজগারের তালাশে এবং বৈধভাবে আনন্দ উপভোগের জন্য”। আরেকটি বর্ণনায় ২য় অংশে ঘুম ও বিশ্রামের উল্লেখ রয়েছে। তার মানে দিনে ৮ ঘন্টার বেশি জব/ডিউটি নয়। ঘুম ও বিশ্রাম মিলেও ৮ ঘন্টার অধিক নয়। স্লিপ মেডিসিনের বইগুলোতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ক্লক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ঘুমের নির্ধারিত সময় রাত ৯ টা থেকে ভোর ৫ টা। দেখুন সুন্নাহ’র সাথে মিলে যায়। এশার সালাতের পর বেহুদা কাজ বা গল্প করা মাকরুহ। আর সারাবছর জুড়ে ভোর ৫ টার আশেপাশেই ফজরের ওয়াক্ত থাকে। সুন্নাহ অনুযায়ী ঘুমের ৩ ধরণের হুকুম পাওয়া যায়-
১. এশার সালাত জামায়াতে পড়ে ঘুমিয়ে গেলে ও ঘুম থেকে জেগে ফজরের সালাত জামায়াতে আদায় করলে সারারাত জেগে নফল ইবাদাতের সওয়াব।
২. রাতের কিছু অংশ জেগে ইলমের অন্বেষণ করলে সারারাত নফল ইবাদাতের সওয়াব। সুতরাং জ্ঞানার্জনের স্বার্থে রাত জাগা যাবে।
৩. দ্রুত ঘুমিয়ে গিয়ে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এরজন্য প্রয়োজনে দুপুরে কাইলুলা বা ভাতঘুম (Napping)
অন্যের জন্য কিংবা অন্যদিনের জন্য কাজ ফেলে রাখবেন না। আগামিকালের বাহানা দেবেন না। আল্লাহর সাহায্য চাইবেন। “আর কোন কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, ‘নিশ্চয় আমি তা আগামী কাল করব’, তবে যদি আল্লাহ চান” (কাহাফ ২৩-২৪)।
পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিং: এটি দুধরণের হতে পারে। আত্মপর্যবেক্ষণ (Self monitoring) বা অন্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকা (Monitoring by mentors)। মুমিন সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পর্যবেক্ষণে থাকে। এই চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে। “অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কেরা” (ইনফিতার ১০)। তবে ইসলামে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিনের আত্মিক উন্নতি ও পর্যবেক্ষণের জন্য একজন মেন্টর খুব জরুরি। দ্বীন শেখা ও প্রচারের জন্য সালাফদের সময় থেকেই এই রেওয়াজ আছে। রাসুলুল্লাহ সা. গভীর রাতে সাহাবিদের কিয়ামুল লাইল ও কুর’আন তিলাওয়াত পর্যবেক্ষণ করতেন এবং ফজরের পরে তাদের নসিহত করতেন। পরিবারের প্রধান যেহেতু মুত্তাকি সদস্যদের ইমাম (ফুরকান ৭৪) বা মেন্টর, তিনিও পরিবারের অন্দরে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। একটি দৈনিক রিপোর্টিং সিস্টেম থাকতে পারে। ব্যক্তিগত রিপোর্ট পদ্ধতি আধুনিককালের হলেও এর স্পিরিট কুর’আন-হাদিস উৎসারিত। মনোরোগের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় দৈনিক রিপোর্ট সংরক্ষণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপসর্গ ট্র্যাক করা হয়। দৈনিক রিপোর্টের মাধ্যমে ব্যক্তি Self monitoring করতে পারে। অথবা দৈনিক কাজ বা পরিকল্পনার চেকলিস্ট থাকতে পারে। যেটি দেখে আপনি নিজেকে মনিটরিং করবেন। কাজ সম্পাদন হলে স্টার মার্ক (*) দেবেন। এই আত্মপর্যবেক্ষণ আত্মিক উন্নতির জন্য জরুরি। ইমাম গাজালি তাঁর ‘এহইয়া উলুমুদ্দীন’ গ্রন্থে আত্মশুদ্ধির জন্য ৬টি কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
১. মুশারাতা; নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজের সাথে চুক্তি করা।
২. মুরাকাবা; রক্ষা করা বা পাহারা দেয়া। নিজের আমলের সংরক্ষণ করা, নিজেকে নিজে পাহারা দিয়ে নফস ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা।
৩. মুহাসাবা; আত্মসমালোচনা করা। নিজের জীবন ও কর্মের প্রতি সব সময় সমালোচনার দৃষ্টি রাখা। সংশোধন হওয়া।
৪. মু’আকাবা; নিজেকে শাস্তি দেয়া। নিজের সাথে কৃত চুক্তি পূরণে ব্যর্থ হলে নফল রোযা, সালাত, সাদাকার মাধ্যমে নফসকে শাস্তি দেয়া।
৫. মুজাহাদা; নফসের খায়েশের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় নিরন্তর জিহাদ বা সংগ্রাম করা।
৬. মুয়াতাবা; সর্বদা তাওবা ও অনুশোচনার হালতে থাকা। মন্দকাজ করলে কালবিলম্ব না করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ভুল স্বীকার করে তাওবা করতে হবে। পুনরায় সেটি না করার সংকল্প করতে হবে।
যাচাই: সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আত্মযাচাই বা Self evaluation. ইমাম গাজালি যাকে মোহাসাবা বলেছেন। দিনের অন্তে নিজেকে একান্তে কিছু সময় মোহাসাবার জন্য রাখতে হবে। কারণ “তোমার কাছে হিসাব চাওয়ার আগে নিজের হিসাব করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ করার আগে নিজেই নিজের কাজের পরিমাপ করে নাও” (তিরমিজি, ৬৩)। নিজের কাজ মূল্যায়ন করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আশানুরূপ ফলাফলে মাঝেমধ্যে নিজেকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে (Self reward)। আবার গুনাহের কাজ হয়ে গেলে নফল রোজা বা সাদাকার মাধ্যমে মু’আকাবা (Self punishment)করা যেতে পারে।
শেষ কথা:
* সময় ব্যবস্থাপনা আপনার লাইফস্টাইল ব্যবস্থাপনার অংশ এবং বলতে গেলে পুরোটাই। সময়মত ঘুম, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম, বিনোদন, কর্মঘন্টা পালন করুন।
* অলসতা পরিহার করুন।
* সময়ের অপচয় না করলে সময়ের অভাব হবে না।
* Odd সময়কে কাজে লাগান।
*সোশ্যাল মিডিয়ায় যৌক্তিক ও পরিকল্পিত সময় দিন।
* গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এলার্ম, রিমাইন্ডার কিংবা এলার্ট মেসেজ চালু রাখুন।
* অবসরে ইবাদাতে মশগুল হোন (ইনশিরাহ ৭-৮)।
* নিজের জন্য সময় রাখুন। পরিবারকে সময় দিন।
* সকাল-সন্ধ্যা যিকর করুন (আহযাব ৪১)।
* কিয়ামতের দিন সময়ের হিসাব দিতে হবে- এটি বারবার স্মরণ করুন।